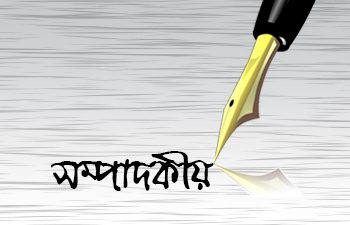স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বাড়ানোর সঙ্গে সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন

স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বাড়ানোর সঙ্গে সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন
সম্পাদকীয়
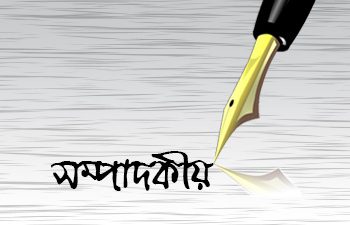
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন। আর এ নিয়ে প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার পর ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। কারণ এই অপর্যাপ্ত বরাদ্দের সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে দেশের মানুষের মোট খরচের ৬৭ শতাংশেরও বেশি বহন করতে হয় নিজেদের পকেট থেকে। এই বিপুল খরচের কারণে প্রতি বছর দেশের প্রায় ৮৬ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে দিচ্ছে। পরিবারে কারও কোনো জটিল রোগ হলেই একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কয়েক প্রজন্মের জন্য ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে যায়। এই সংকট কিছুটা লাঘব করার জন্য বাজেট বৃদ্ধি এবং লোকবল নিয়োগ জরুরি, সেটা সত্য। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ আর লোকবল নিয়োগ করলেই সমস্যার প্রত্যাশিত সমাধান আসবে না। বাস্তবে পরিকল্পনাহীনভাবে বাজেট বৃদ্ধি এবং গণহারে লোকবল নিয়োগ স্বাস্থ্য খাতের মৌলিক সমস্যাগুলো যেমন অদক্ষতা ও দুর্নীতির মতো বিদ্যমান সমস্যার সমাধান না করে বরং সেগুলোকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) নির্দেশনা অনুযায়ী, একটি দেশের বাজেটের ১৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দ কথা থাকলেও বাংলাদেশে ৫ শতাংশের কাছাকাছি। আবার দেখা যাচ্ছে নানা কারণে এই ৫ শতাংশ বরাদ্দের একটি বড়ো অংশ খরচ করা সম্ভব হচ্ছে না। আইটেম অনুযায়ী বাজেট হওয়ায় এ সমস্যা হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই স্বাস্থ্য খাতের বাজেট ৫ শতাংশের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সে তুলনায় বাজেটটা অনেক কম। বাজেটের দুটি অংশ থাকে, যথা-রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নানা কারণে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন বাজেটের একটা বড় অংশ খরচ হয় না। এর পরিমাণ ২৫-৩৫ শতাংশ। ফলে প্রতি বছর বাজেট ঘোষণার পর একটি অংশ বলেন স্বাস্থ্য খাতে বাজেট অনেক কম দেওয়া হয়েছে। আবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, যে বাজেট দেওয়া হয়েছে তা থেকেই তো খরচ হয় না, তাহলে অতিরিক্ত বাজেট দিয়ে লাভ কি? শুধু বাজেটের আকার বাড়লেই যে ভালো সেবা পাওয়া যাবে তা না, বরং সঠিক উপায়ে এটি খরচ করতে হবে। বাজেট খরচ না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ খালি থাকা। ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্ট-২০২০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে যে হেলথ ফাইনান্সিং হচ্ছে তার ৬৯ শতাংশ ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ হচ্ছে। সেখানে সরকারের খরচ মাত্র ২৩ শতাংশ। সরকারের তরফ থেকে খরচের দিক থেকে এ পরিমাণ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম। ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ হওয়া ৬৯ শতাংশের একটা বড়ো অংশ যাচ্ছে ওষুধে, এরপর প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খরচ হচ্ছে প্রায় ১২ শতাংশের মতো। অবশ্য ব্যক্তির পকেট এত বড়ো একটা অংশ খরচ হওয়ার অন্যতম কারণ, আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ কারণে ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ অনেক বেশি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য এখন শুধু ‘আরও বাজেট’ই সমাধান নয়। অপরিকল্পিত বাজেট বৃদ্ধি রাজনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় কিন্তু টেকসই সমাধান নয়। স্বাস্থ্য খাতকে সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী করতে হলে এর দর্শনে পরিবর্তন করতে হবে। চিকিৎসাকেন্দ্রিক মডেল থেকে প্রতিরোধকেন্দ্রিক মডেলে যেতে হবে।
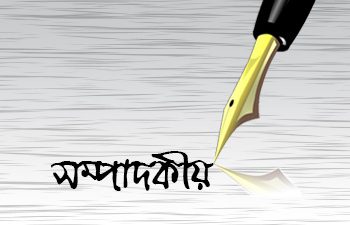
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন। আর এ নিয়ে প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার পর ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। কারণ এই অপর্যাপ্ত বরাদ্দের সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে দেশের মানুষের মোট খরচের ৬৭ শতাংশেরও বেশি বহন করতে হয় নিজেদের পকেট থেকে। এই বিপুল খরচের কারণে প্রতি বছর দেশের প্রায় ৮৬ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে দিচ্ছে। পরিবারে কারও কোনো জটিল রোগ হলেই একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কয়েক প্রজন্মের জন্য ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে যায়। এই সংকট কিছুটা লাঘব করার জন্য বাজেট বৃদ্ধি এবং লোকবল নিয়োগ জরুরি, সেটা সত্য। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ আর লোকবল নিয়োগ করলেই সমস্যার প্রত্যাশিত সমাধান আসবে না। বাস্তবে পরিকল্পনাহীনভাবে বাজেট বৃদ্ধি এবং গণহারে লোকবল নিয়োগ স্বাস্থ্য খাতের মৌলিক সমস্যাগুলো যেমন অদক্ষতা ও দুর্নীতির মতো বিদ্যমান সমস্যার সমাধান না করে বরং সেগুলোকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) নির্দেশনা অনুযায়ী, একটি দেশের বাজেটের ১৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দ কথা থাকলেও বাংলাদেশে ৫ শতাংশের কাছাকাছি। আবার দেখা যাচ্ছে নানা কারণে এই ৫ শতাংশ বরাদ্দের একটি বড়ো অংশ খরচ করা সম্ভব হচ্ছে না। আইটেম অনুযায়ী বাজেট হওয়ায় এ সমস্যা হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই স্বাস্থ্য খাতের বাজেট ৫ শতাংশের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সে তুলনায় বাজেটটা অনেক কম। বাজেটের দুটি অংশ থাকে, যথা-রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নানা কারণে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন বাজেটের একটা বড় অংশ খরচ হয় না। এর পরিমাণ ২৫-৩৫ শতাংশ। ফলে প্রতি বছর বাজেট ঘোষণার পর একটি অংশ বলেন স্বাস্থ্য খাতে বাজেট অনেক কম দেওয়া হয়েছে। আবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, যে বাজেট দেওয়া হয়েছে তা থেকেই তো খরচ হয় না, তাহলে অতিরিক্ত বাজেট দিয়ে লাভ কি? শুধু বাজেটের আকার বাড়লেই যে ভালো সেবা পাওয়া যাবে তা না, বরং সঠিক উপায়ে এটি খরচ করতে হবে। বাজেট খরচ না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ খালি থাকা। ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্ট-২০২০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে যে হেলথ ফাইনান্সিং হচ্ছে তার ৬৯ শতাংশ ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ হচ্ছে। সেখানে সরকারের খরচ মাত্র ২৩ শতাংশ। সরকারের তরফ থেকে খরচের দিক থেকে এ পরিমাণ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম। ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ হওয়া ৬৯ শতাংশের একটা বড়ো অংশ যাচ্ছে ওষুধে, এরপর প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খরচ হচ্ছে প্রায় ১২ শতাংশের মতো। অবশ্য ব্যক্তির পকেট এত বড়ো একটা অংশ খরচ হওয়ার অন্যতম কারণ, আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ কারণে ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ অনেক বেশি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য এখন শুধু ‘আরও বাজেট’ই সমাধান নয়। অপরিকল্পিত বাজেট বৃদ্ধি রাজনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় কিন্তু টেকসই সমাধান নয়। স্বাস্থ্য খাতকে সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী করতে হলে এর দর্শনে পরিবর্তন করতে হবে। চিকিৎসাকেন্দ্রিক মডেল থেকে প্রতিরোধকেন্দ্রিক মডেলে যেতে হবে।