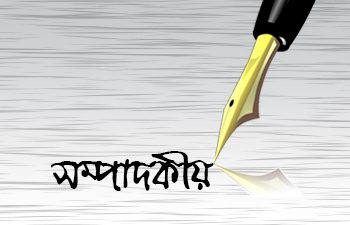বাংলাদেশের স্থানিক পরিকল্পনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা

বাংলাদেশের স্থানিক পরিকল্পনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা
সম্পাদকীয়
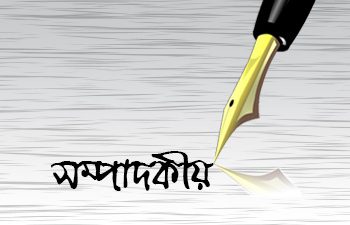
দেশের ভূমি ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও নগরায়ণ আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে নতুন চিন্তা ও কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগে যে বড় ধরনের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা এই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। দীর্ঘদিন ধরেই দেশের বেশিরভাগ উন্নয়নকাজ-বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামো নির্মাণ-পরিকল্পনাবিহীনভাবে হয়ে এসেছে। সড়ক ও জনপথ, এলজিইডি, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করলেও তাদের কাঠামোয় যথাযথ পরিকল্পনাবিদের অভাবের কারণে সার্বিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ঘাটতি থেকেই গেছে। ফলাফল-অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কৃষিজমির উপর অনিয়ন্ত্রিত চাপ এবং জাতীয় সম্পদের অপচয়। রাষ্ট্রের জন্য এ পরিস্থিতির ঝুঁকি ছোট নয়। ১৯৭১ সালে যেখান থেকে ৬৮ শতাংশ জমি ছিল আবাদযোগ্য, তা এখন কমে ৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; মাথাপিছু জমিও কমেছে তিনগুণের বেশি। এর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যুক্ত হয়ে ১০ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। এই বাস্তবতায় ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি ব্যবহার কীভাবে হবে, তা নির্ধারণ করা শুধু উন্নয়ন নয়-বরং টিকে থাকার প্রাথমিক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনটি নতুন দপ্তর-স্থানিক পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্থানিক পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্থানিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি-গঠনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও সরকার এগুলোকে দুটি দপ্তরে একীভূত করার চিন্তাভাবনা করছে, মূল উদ্দেশ্য একই-দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নির্ভুল, সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা। উপজেলা ও পৌর এলাকার বাস্তব চিত্র আরও উদ্বেগজনক। এলজিইডি এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি পৌরসভার স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পেরেছে, যখন দেশের ৯৬ শতাংশেরও বেশি এলাকা কার্যত পরিকল্পনাবিহীনভাবে বেড়ে উঠছে। এর ফলে এলোমেলো হাটবাজার, অবকাঠামো, শিল্পকারখানা এবং আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে-যা ভবিষ্যতে নগর ও গ্রাম উভয়ের টেকসই উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। নতুন কাঠামোয় যে বিষয়টি বিশেষভাবে আশাব্যঞ্জক, তা হলো-পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল দায়িত্ব থাকবে প্রশিক্ষিত ও যোগ্য পরিকল্পনাবিদদের হাতে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও পরিকল্পনার বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে এটি সহায়তা করবে। তবে এই উদ্যোগ নিয়ে কিছু প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে আসে। পরিকল্পনার এই কাঠামো জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে নতুন জটিলতা তৈরি করবে কি না-তা এখনই বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইভাবে ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার দ্বৈততা বা আন্তঃদপ্তরীয় সংঘাত যেন পুরো পরিকল্পনাকে ব্যাহত না করে, সেদিকেও সতর্ক থাকা জরুরি। সুতরাং, যে বাস্তবতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট: বাংলাদেশ আর অপরিকল্পিত উন্নয়নের ঝুঁকি বহন করতে পারে না। একটি পরিকল্পিত দেশ গড়তে হলে স্থানিক পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক এবং এই সংস্কার তারই ভিত্তিপ্রস্তর। এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সুচিন্তিত বাস্তবায়ন। শুধু কাঠামো গঠন করলেই হবে না; প্রতিটি পরিকল্পনা যেন বাস্তবের সঙ্গে মিল রেখে কার্যকর হয়, সেটিই হবে আগামী দিনের মূল চ্যালেঞ্জ।
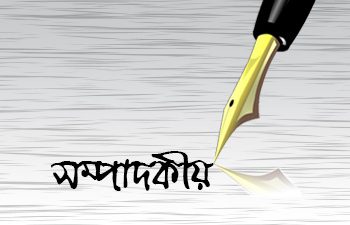
দেশের ভূমি ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও নগরায়ণ আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে নতুন চিন্তা ও কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগে যে বড় ধরনের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা এই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। দীর্ঘদিন ধরেই দেশের বেশিরভাগ উন্নয়নকাজ-বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামো নির্মাণ-পরিকল্পনাবিহীনভাবে হয়ে এসেছে। সড়ক ও জনপথ, এলজিইডি, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করলেও তাদের কাঠামোয় যথাযথ পরিকল্পনাবিদের অভাবের কারণে সার্বিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ঘাটতি থেকেই গেছে। ফলাফল-অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কৃষিজমির উপর অনিয়ন্ত্রিত চাপ এবং জাতীয় সম্পদের অপচয়। রাষ্ট্রের জন্য এ পরিস্থিতির ঝুঁকি ছোট নয়। ১৯৭১ সালে যেখান থেকে ৬৮ শতাংশ জমি ছিল আবাদযোগ্য, তা এখন কমে ৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; মাথাপিছু জমিও কমেছে তিনগুণের বেশি। এর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যুক্ত হয়ে ১০ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। এই বাস্তবতায় ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি ব্যবহার কীভাবে হবে, তা নির্ধারণ করা শুধু উন্নয়ন নয়-বরং টিকে থাকার প্রাথমিক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনটি নতুন দপ্তর-স্থানিক পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্থানিক পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্থানিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি-গঠনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও সরকার এগুলোকে দুটি দপ্তরে একীভূত করার চিন্তাভাবনা করছে, মূল উদ্দেশ্য একই-দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নির্ভুল, সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা। উপজেলা ও পৌর এলাকার বাস্তব চিত্র আরও উদ্বেগজনক। এলজিইডি এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি পৌরসভার স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পেরেছে, যখন দেশের ৯৬ শতাংশেরও বেশি এলাকা কার্যত পরিকল্পনাবিহীনভাবে বেড়ে উঠছে। এর ফলে এলোমেলো হাটবাজার, অবকাঠামো, শিল্পকারখানা এবং আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে-যা ভবিষ্যতে নগর ও গ্রাম উভয়ের টেকসই উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। নতুন কাঠামোয় যে বিষয়টি বিশেষভাবে আশাব্যঞ্জক, তা হলো-পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল দায়িত্ব থাকবে প্রশিক্ষিত ও যোগ্য পরিকল্পনাবিদদের হাতে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও পরিকল্পনার বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে এটি সহায়তা করবে। তবে এই উদ্যোগ নিয়ে কিছু প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে আসে। পরিকল্পনার এই কাঠামো জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে নতুন জটিলতা তৈরি করবে কি না-তা এখনই বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইভাবে ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার দ্বৈততা বা আন্তঃদপ্তরীয় সংঘাত যেন পুরো পরিকল্পনাকে ব্যাহত না করে, সেদিকেও সতর্ক থাকা জরুরি। সুতরাং, যে বাস্তবতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট: বাংলাদেশ আর অপরিকল্পিত উন্নয়নের ঝুঁকি বহন করতে পারে না। একটি পরিকল্পিত দেশ গড়তে হলে স্থানিক পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক এবং এই সংস্কার তারই ভিত্তিপ্রস্তর। এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সুচিন্তিত বাস্তবায়ন। শুধু কাঠামো গঠন করলেই হবে না; প্রতিটি পরিকল্পনা যেন বাস্তবের সঙ্গে মিল রেখে কার্যকর হয়, সেটিই হবে আগামী দিনের মূল চ্যালেঞ্জ।