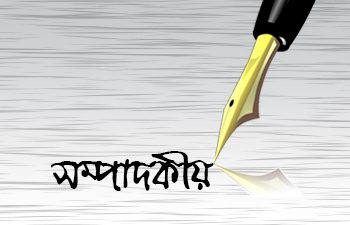বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায়
নষ্ট আস্থা ফিরিয়ে আনা

বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায়
মো: শামীম মিয়া

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক সংকটকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার গভীরতা অনেকের ধারণার চেয়েও বেশি। দেশজুড়ে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, রপ্তানি আয় হ্রাস পাচ্ছে, শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মসংস্থান সংকুচিত হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তলানিতে ঠেকেছে। অথচ কোনো দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তিই হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগ ছাড়া কর্মসংস্থান হয় না, কর্মসংস্থান ছাড়া আয় বাড়ে না, আয় না বাড়লে উন্নয়ন কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাই একটাই কথা বলছে-যত দ্রুত সম্ভব বিনিয়োগের জন্য আস্থাশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, অন্যথায় এই সংকট দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতায় রূপ নেবে।
ক্রমেই গভীর হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক সংকট। একের পর এক চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকারত্বের হার দ্রুত বাড়ছে। অনেক কারখানা বন্ধ না হলেও টিকে থাকার লড়াইয়ে ধুঁকে ধুঁকে চলছে। উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে রপ্তানি আয় হ্রাস পাচ্ছে, রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে, সরকার বাধ্য হচ্ছে ঋণের ওপর নির্ভরশীল হতে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেই রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ হাজার ৮৯৯ কোটি টাকা, যা অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতিফলন। এই ঘাটতি শুধু সরকারের আয় কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয় না, বরং দেখিয়ে দেয় ব্যাবসাবাণিজ্যের স্থবিরতা এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার বাস্তবতাকে।
২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ঢালাওভাবে শিল্পমালিক ও উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলা, মিথ্যা অভিযোগ, হামলা, মব সন্ত্রাস, কারখানা দখল, চাঁদাবাজি ও অগ্নিসংযোগের মতো বহু ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান তাদের বিনিয়োগ স্থগিত রেখেছে কিংবা অন্য দেশে সরিয়ে নিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্বালানি সংকট। গ্যাস-বিদ্যুতের অভাবের কারণে শিল্পাঞ্চলগুলোতে উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, তারা মাসের পর মাস প্রোডাকশন হাফ করে দিচ্ছেন কারণ গ্যাস চাপ কম, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বেশি, আর বিকল্প জ্বালানি ব্যয়বহুল। ফলে তারা ধীরে ধীরে ক্ষতির মুখে পড়ছেন।
অন্যদিকে ঋণের উচ্চ সুদহার ব্যবসায়ীদের জন্য ভয়াবহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৩১৪ শতাংশ পর্যন্ত সুদে ব্যাংক ঋণ নিয়ে কেউ নতুন প্রকল্পে হাত দিতে সাহস পাচ্ছেন না। এতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে না, পুরোনো উদ্যোগের সম্প্রসারণও বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ যেভাবে সংকুচিত হচ্ছে, তাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়, বরং বেকারত্ব বাড়ছে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং সিদ্ধান্তহীনতা বিনিয়োগের পথে বড়ো বাধা হয়ে উঠেছে।
বিশ্বের বিনিয়োগ ঝুঁকি সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। বৈশ্বিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের ‘গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইনডেক্স’-এ ২২৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯৩তম। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে আমরা পঞ্চম, আমাদের পেছনে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। এই পরিসংখ্যান কেবল সংখ্যা নয়, এটি আমাদের বিনিয়োগ আস্থার চিত্র তুলে ধরে। একই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বৈশ্বিক পাসপোর্ট সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান নেমে এসেছে ১০০তম স্থানে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে।
বিনিয়োগকারীরা যেখানেই যান না কেন, তারা তিনটি বিষয় খোঁজেন-স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা। দীর্ঘ মেয়াদে কেউই সেই দেশে বিনিয়োগ করতে চান না, যেখানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। বাংলাদেশে এই তিন দিকেই বড়ো সংকট দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়া দখল, অর্থনীতির ওপর প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক লুট ও অর্থ পাচারের মাধ্যমে অর্থনীতির ভেতরের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করা হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার ও তার পারিবারিক গোষ্ঠী ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। ব্যাংকের টাকা লোপাট, শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয়, ব্যবসায়ীদের ওপর দমননীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সংস্কৃতি মিলিয়ে এক ভয়াবহ অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।
২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর যে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, তারা এখন পর্যুদস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কাজ করছে। অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে চেষ্টা করছেন রিজার্ভ বাড়াতে, রেমিট্যান্স প্রবাহ স্থিতিশীল করতে এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বাড়াতে। কিন্তু এখনো সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগ পুনরুজ্জীবিত করা। কারণ বিনিয়োগকারীরা এখনো আস্থাহীনতায় ভুগছেন। তারা ভাবছেন, এই অন্তর্বর্তী সরকারের পর যে স্থায়ী রাজনৈতিক সরকার আসবে, তারা কতটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাই প্রধান কাজ। আস্থা তৈরি হয় রাজনৈতিক স্থিতি, সুশাসন, স্বচ্ছ নীতি ও আইনের শাসনের মাধ্যমে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা এই জায়গাতেই। দুর্নীতি, ঘুষ, তদবির, কমিশন সংস্কৃতি, সরকারি দপ্তরে সিদ্ধান্তহীনতা-সব মিলিয়ে উদ্যোক্তারা মনে করেন, এখানে সততা নয়, প্রভাবই সব। এমন মানসিকতার রাষ্ট্রে কেউ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে না।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাসে দেখা গেছে, যখনই সরকার ব্যাবসাবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে, বিনিয়োগ বেড়েছে। নব্বইয়ের দশকে বেসরকারিকরণ, ২০০০ সালের পর পোশাক শিল্পে প্রণোদনা এবং অবকাঠামো খাতে করছাড় নীতি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু গত এক দশকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ ও নীতির অনিশ্চয়তা সেই ধারা ভেঙে দিয়েছে। এখনকার বাস্তবতায় নতুন উদ্যোগ, প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ, কিংবা রপ্তানিমুখী শিল্প-সবখানেই উদ্যোক্তারা পিছু হটছেন।
বিনিয়োগ শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি সামাজিক পরিবর্তনেরও হাতিয়ার। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে সমাজে স্থিতি আসে, দারিদ্র্য কমে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়ে। কিন্তু বর্তমানে বেকারত্ব বাড়ায় সামাজিক অসন্তোষ বাড়ছে, তরুণদের মধ্যে হতাশা গভীর হচ্ছে। দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, অথচ নতুন চাকরি তৈরি হয় সর্বোচ্চ ৭ থেকে ৮ লাখ। বাকি অংশ হয় বেকার বা বিদেশগামী। বিদেশে শ্রম রপ্তানিও এখন ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। ফলে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের একমাত্র পথ হচ্ছে বিনিয়োগ।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে-বিনিয়োগের এই আস্থাহীনতা কীভাবে কাটানো যায়? প্রথমত, সরকারকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে কেউ ঝুঁকি নেবে না। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং খাত সংস্কার করতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা, ঋণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নীতি সহায়তা দিতে হবে। তৃতীয়ত, জ্বালানি সংকট নিরসনে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। শিল্পাঞ্চলগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত না হলে উৎপাদন টিকবে না। চতুর্থত, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ঘুষ সংস্কৃতি কমাতে ডিজিটাল প্রশাসন এবং স্বয়ংক্রিয় অনুমোদন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
এ ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে কার্যকর করতে হবে। বর্তমানে ঘোষিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অর্ধেকই অচল বা স্থবির। ভূমি, অবকাঠামো, করছাড়, শ্রমনীতি-সবকিছুতে একক জানালা নীতি চালু করা গেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আন্তর্জাতিক আস্থা ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক পর্যায়ে বিনিয়োগবান্ধব ইমেজ গড়ে তোলাও জরুরি।
বিনিয়োগকে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি বলা হয়, কারণ এটি অর্থনীতির সব খাতকে সচল রাখে। শিল্প খাতে বিনিয়োগ মানে কাঁচামাল, পরিবহন, বিমা, ব্যাংকিং, এমনকি কৃষিতেও প্রভাব ফেলে। এক ডলার বিনিয়োগে প্রায় তিন ডলার মূল্য সংযোজন হয়-এই সূত্রেই বোঝা যায় বিনিয়োগের শক্তি কতটা বিস্তৃত। তাই সরকার যদি সত্যিই দেশের জীবনমান উন্নত করতে চায়, তবে প্রথমেই তাকে বিনিয়োগ পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
বর্তমান সরকারের সময় যদি বিনিয়োগ না বাড়ে, তবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কারণ এই সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ও পেশাদার উপদেষ্টারা, যাদের হাতে সুযোগ আছে বিনিয়োগবান্ধব নীতি তৈরি করার। তাদের উচিত সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা-যেখানে থাকবে বিনিয়োগ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, নীতি প্রণোদনা, কর সংস্কার, শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের রোডম্যাপ।
সবচেয়ে বড়ো কথা, বিনিয়োগে আস্থা ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য। বিনিয়োগকারীকে প্রতিপক্ষ নয়, অংশীদার হিসেবে দেখতে হবে। যেই দেশে ব্যবসায়ীরা ভয় পায়, সেই দেশ কখনো উন্নত হয় না। তাই সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত আস্থা তৈরি করা-যাতে বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারেন, তাদের পুঁজি, শ্রম ও চিন্তা নিরাপদ হাতে আছে। বিনিয়োগের এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে পরবর্তী সরকার এলেও নীতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং ব্যাবসার স্থিতিশীলতা অটুট থাকবে।
অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের এই যাত্রায় আমাদের এখন প্রয়োজন দূরদর্শী পরিকল্পনা, প্রশাসনিক সততা এবং রাজনৈতিক ঐক্য। বিনিয়োগ ছাড়া কোনো উন্নয়ন স্থায়ী হয় না। তাই এখনই সময় বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নেওয়ার-যাতে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবারও প্রাণ ফিরে পায়, তরুণদের হাতে কর্মসংস্থান ফিরে আসে, আর বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা জাগে যে এই দেশ এখনও সম্ভাবনার। বাংলাদেশের মতো ১৮ কোটির মানুষের দেশে বিনিয়োগই পারে ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণ করতে। একে রাজনৈতিক খেলার বল বানিয়ে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখতে হবে। সময় এখনই-নাহলে দেরি হয়ে যাবে। অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে হলে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করতেই হবে, কারণ বিনিয়োগই উন্নয়ন, বিনিয়োগই স্থিতিশীলতা, আর বিনিয়োগই একমাত্র পথ যা মানুষকে বেকারত্ব ও হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারে।
লেখক: মো: শামীম মিয়া; কলামিস্ট

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক সংকটকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার গভীরতা অনেকের ধারণার চেয়েও বেশি। দেশজুড়ে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, রপ্তানি আয় হ্রাস পাচ্ছে, শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মসংস্থান সংকুচিত হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তলানিতে ঠেকেছে। অথচ কোনো দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তিই হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগ ছাড়া কর্মসংস্থান হয় না, কর্মসংস্থান ছাড়া আয় বাড়ে না, আয় না বাড়লে উন্নয়ন কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাই একটাই কথা বলছে-যত দ্রুত সম্ভব বিনিয়োগের জন্য আস্থাশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, অন্যথায় এই সংকট দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতায় রূপ নেবে।
ক্রমেই গভীর হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক সংকট। একের পর এক চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকারত্বের হার দ্রুত বাড়ছে। অনেক কারখানা বন্ধ না হলেও টিকে থাকার লড়াইয়ে ধুঁকে ধুঁকে চলছে। উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে রপ্তানি আয় হ্রাস পাচ্ছে, রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে, সরকার বাধ্য হচ্ছে ঋণের ওপর নির্ভরশীল হতে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেই রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ হাজার ৮৯৯ কোটি টাকা, যা অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতিফলন। এই ঘাটতি শুধু সরকারের আয় কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয় না, বরং দেখিয়ে দেয় ব্যাবসাবাণিজ্যের স্থবিরতা এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার বাস্তবতাকে।
২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ঢালাওভাবে শিল্পমালিক ও উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলা, মিথ্যা অভিযোগ, হামলা, মব সন্ত্রাস, কারখানা দখল, চাঁদাবাজি ও অগ্নিসংযোগের মতো বহু ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান তাদের বিনিয়োগ স্থগিত রেখেছে কিংবা অন্য দেশে সরিয়ে নিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্বালানি সংকট। গ্যাস-বিদ্যুতের অভাবের কারণে শিল্পাঞ্চলগুলোতে উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, তারা মাসের পর মাস প্রোডাকশন হাফ করে দিচ্ছেন কারণ গ্যাস চাপ কম, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বেশি, আর বিকল্প জ্বালানি ব্যয়বহুল। ফলে তারা ধীরে ধীরে ক্ষতির মুখে পড়ছেন।
অন্যদিকে ঋণের উচ্চ সুদহার ব্যবসায়ীদের জন্য ভয়াবহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৩১৪ শতাংশ পর্যন্ত সুদে ব্যাংক ঋণ নিয়ে কেউ নতুন প্রকল্পে হাত দিতে সাহস পাচ্ছেন না। এতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে না, পুরোনো উদ্যোগের সম্প্রসারণও বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ যেভাবে সংকুচিত হচ্ছে, তাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়, বরং বেকারত্ব বাড়ছে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং সিদ্ধান্তহীনতা বিনিয়োগের পথে বড়ো বাধা হয়ে উঠেছে।
বিশ্বের বিনিয়োগ ঝুঁকি সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। বৈশ্বিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের ‘গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইনডেক্স’-এ ২২৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯৩তম। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে আমরা পঞ্চম, আমাদের পেছনে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। এই পরিসংখ্যান কেবল সংখ্যা নয়, এটি আমাদের বিনিয়োগ আস্থার চিত্র তুলে ধরে। একই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বৈশ্বিক পাসপোর্ট সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান নেমে এসেছে ১০০তম স্থানে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে।
বিনিয়োগকারীরা যেখানেই যান না কেন, তারা তিনটি বিষয় খোঁজেন-স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা। দীর্ঘ মেয়াদে কেউই সেই দেশে বিনিয়োগ করতে চান না, যেখানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। বাংলাদেশে এই তিন দিকেই বড়ো সংকট দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়া দখল, অর্থনীতির ওপর প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক লুট ও অর্থ পাচারের মাধ্যমে অর্থনীতির ভেতরের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করা হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার ও তার পারিবারিক গোষ্ঠী ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। ব্যাংকের টাকা লোপাট, শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয়, ব্যবসায়ীদের ওপর দমননীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সংস্কৃতি মিলিয়ে এক ভয়াবহ অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।
২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর যে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, তারা এখন পর্যুদস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কাজ করছে। অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে চেষ্টা করছেন রিজার্ভ বাড়াতে, রেমিট্যান্স প্রবাহ স্থিতিশীল করতে এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বাড়াতে। কিন্তু এখনো সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগ পুনরুজ্জীবিত করা। কারণ বিনিয়োগকারীরা এখনো আস্থাহীনতায় ভুগছেন। তারা ভাবছেন, এই অন্তর্বর্তী সরকারের পর যে স্থায়ী রাজনৈতিক সরকার আসবে, তারা কতটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাই প্রধান কাজ। আস্থা তৈরি হয় রাজনৈতিক স্থিতি, সুশাসন, স্বচ্ছ নীতি ও আইনের শাসনের মাধ্যমে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা এই জায়গাতেই। দুর্নীতি, ঘুষ, তদবির, কমিশন সংস্কৃতি, সরকারি দপ্তরে সিদ্ধান্তহীনতা-সব মিলিয়ে উদ্যোক্তারা মনে করেন, এখানে সততা নয়, প্রভাবই সব। এমন মানসিকতার রাষ্ট্রে কেউ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে না।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাসে দেখা গেছে, যখনই সরকার ব্যাবসাবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে, বিনিয়োগ বেড়েছে। নব্বইয়ের দশকে বেসরকারিকরণ, ২০০০ সালের পর পোশাক শিল্পে প্রণোদনা এবং অবকাঠামো খাতে করছাড় নীতি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু গত এক দশকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ ও নীতির অনিশ্চয়তা সেই ধারা ভেঙে দিয়েছে। এখনকার বাস্তবতায় নতুন উদ্যোগ, প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ, কিংবা রপ্তানিমুখী শিল্প-সবখানেই উদ্যোক্তারা পিছু হটছেন।
বিনিয়োগ শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি সামাজিক পরিবর্তনেরও হাতিয়ার। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে সমাজে স্থিতি আসে, দারিদ্র্য কমে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়ে। কিন্তু বর্তমানে বেকারত্ব বাড়ায় সামাজিক অসন্তোষ বাড়ছে, তরুণদের মধ্যে হতাশা গভীর হচ্ছে। দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, অথচ নতুন চাকরি তৈরি হয় সর্বোচ্চ ৭ থেকে ৮ লাখ। বাকি অংশ হয় বেকার বা বিদেশগামী। বিদেশে শ্রম রপ্তানিও এখন ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। ফলে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের একমাত্র পথ হচ্ছে বিনিয়োগ।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে-বিনিয়োগের এই আস্থাহীনতা কীভাবে কাটানো যায়? প্রথমত, সরকারকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে কেউ ঝুঁকি নেবে না। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং খাত সংস্কার করতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা, ঋণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নীতি সহায়তা দিতে হবে। তৃতীয়ত, জ্বালানি সংকট নিরসনে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। শিল্পাঞ্চলগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত না হলে উৎপাদন টিকবে না। চতুর্থত, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ঘুষ সংস্কৃতি কমাতে ডিজিটাল প্রশাসন এবং স্বয়ংক্রিয় অনুমোদন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
এ ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে কার্যকর করতে হবে। বর্তমানে ঘোষিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অর্ধেকই অচল বা স্থবির। ভূমি, অবকাঠামো, করছাড়, শ্রমনীতি-সবকিছুতে একক জানালা নীতি চালু করা গেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আন্তর্জাতিক আস্থা ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক পর্যায়ে বিনিয়োগবান্ধব ইমেজ গড়ে তোলাও জরুরি।
বিনিয়োগকে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি বলা হয়, কারণ এটি অর্থনীতির সব খাতকে সচল রাখে। শিল্প খাতে বিনিয়োগ মানে কাঁচামাল, পরিবহন, বিমা, ব্যাংকিং, এমনকি কৃষিতেও প্রভাব ফেলে। এক ডলার বিনিয়োগে প্রায় তিন ডলার মূল্য সংযোজন হয়-এই সূত্রেই বোঝা যায় বিনিয়োগের শক্তি কতটা বিস্তৃত। তাই সরকার যদি সত্যিই দেশের জীবনমান উন্নত করতে চায়, তবে প্রথমেই তাকে বিনিয়োগ পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
বর্তমান সরকারের সময় যদি বিনিয়োগ না বাড়ে, তবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কারণ এই সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ও পেশাদার উপদেষ্টারা, যাদের হাতে সুযোগ আছে বিনিয়োগবান্ধব নীতি তৈরি করার। তাদের উচিত সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা-যেখানে থাকবে বিনিয়োগ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, নীতি প্রণোদনা, কর সংস্কার, শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের রোডম্যাপ।
সবচেয়ে বড়ো কথা, বিনিয়োগে আস্থা ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য। বিনিয়োগকারীকে প্রতিপক্ষ নয়, অংশীদার হিসেবে দেখতে হবে। যেই দেশে ব্যবসায়ীরা ভয় পায়, সেই দেশ কখনো উন্নত হয় না। তাই সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত আস্থা তৈরি করা-যাতে বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারেন, তাদের পুঁজি, শ্রম ও চিন্তা নিরাপদ হাতে আছে। বিনিয়োগের এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে পরবর্তী সরকার এলেও নীতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং ব্যাবসার স্থিতিশীলতা অটুট থাকবে।
অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের এই যাত্রায় আমাদের এখন প্রয়োজন দূরদর্শী পরিকল্পনা, প্রশাসনিক সততা এবং রাজনৈতিক ঐক্য। বিনিয়োগ ছাড়া কোনো উন্নয়ন স্থায়ী হয় না। তাই এখনই সময় বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নেওয়ার-যাতে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবারও প্রাণ ফিরে পায়, তরুণদের হাতে কর্মসংস্থান ফিরে আসে, আর বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা জাগে যে এই দেশ এখনও সম্ভাবনার। বাংলাদেশের মতো ১৮ কোটির মানুষের দেশে বিনিয়োগই পারে ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণ করতে। একে রাজনৈতিক খেলার বল বানিয়ে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখতে হবে। সময় এখনই-নাহলে দেরি হয়ে যাবে। অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে হলে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করতেই হবে, কারণ বিনিয়োগই উন্নয়ন, বিনিয়োগই স্থিতিশীলতা, আর বিনিয়োগই একমাত্র পথ যা মানুষকে বেকারত্ব ও হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারে।
লেখক: মো: শামীম মিয়া; কলামিস্ট